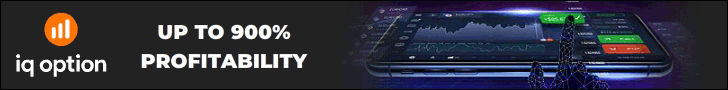ভূমিকম্প
ভূমিকম্প : কারণ, প্রভাব এবং সতর্কতা
ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভূ-গঠন-এর আকস্মিক স্থানচ্যুতি বা কম্পনের ফলে সৃষ্টি হয়। এটি পৃথিবীর পৃষ্ঠে ভূমিকম্প তরঙ্গ আকারে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারে। ভূমিকম্পের কারণ, প্রভাব, সতর্কতা এবং মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:
ভূমিকম্পের কারণ
ভূমিকম্পের প্রধান কারণগুলো হলো:
- ভূ-পেশীর চলন (Tectonic Plate Movement): পৃথিবীর ভূত্বক (Crust) বেশ কয়েকটি বিশাল খণ্ডে বিভক্ত, যেগুলোকে ভূ-পেশী (Tectonic Plate) বলা হয়। এই প্লেটগুলো constantly motion-এ থাকে। যখন দুটি প্লেট একে অপরের দিকে অগ্রসর হয় (convergent boundary), একে অপরের থেকে দূরে সরে যায় (divergent boundary) অথবা একে অপরের পাশ দিয়ে চলে যায় (transform boundary), তখন সংঘর্ষের ফলে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তি ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে। ভূ-পেশী তত্ত্ব এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।
- আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত (Volcanic Eruption): আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূগর্ভের চাপ বৃদ্ধি পায়, যা ভূমিকম্পের কারণ হতে পারে। তবে এই ধরনের ভূমিকম্প সাধারণত স্থানীয় এবং কম তীব্রতার হয়।
- ভূগর্ভস্থ শিলাচ্যুতি (Faulting): ভূগর্ভের শিলাস্তরে ফাটল বা চ্যুতি (Fault) বরাবর শিলার স্থানচ্যুতি ভূমিকম্পের অন্যতম কারণ।
- ভূগর্ভস্থ জলের চাপ (Underground Water Pressure): কিছু ক্ষেত্রে, ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত চাপ শিলাস্তরের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে।
- মানব সৃষ্ট কারণ (Human Induced Seismicity): খনন কাজ, তেল ও গ্যাস উত্তোলনের সময়, অথবা বড় ড্যাম নির্মাণের ফলে ভূগর্ভের চাপ পরিবর্তিত হয়ে ভূমিকম্প হতে পারে।
ভূমিকম্পের প্রকারভেদ
ভূমিকম্পকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়:
- উৎপত্তির গভীরতার ভিত্তিতে:
* অল্প গভীরতার ভূমিকম্প (Shallow-focus Earthquake): ৭০ কিলোমিটারের কম গভীরতায় উৎপন্ন হয়। এগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। * মধ্য গভীরতার ভূমিকম্প (Intermediate-focus Earthquake): ৭০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার গভীরতায় উৎপন্ন হয়। * গভীর গভীরতার ভূমিকম্প (Deep-focus Earthquake): ৩০০ কিলোমিটারের বেশি গভীরতায় উৎপন্ন হয়। এগুলোর তীব্রতা কম থাকে।
- কারণ অনুসারে:
* টেকটোনিক ভূমিকম্প (Tectonic Earthquake): ভূ-পেশীর চলন বা সংঘর্ষের কারণে সৃষ্ট। * আগ্নেয় ভূমিকম্প (Volcanic Earthquake): আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সৃষ্ট। * সংবেদী ভূমিকম্প (Induced Earthquake): মানুষের কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট।
- তীব্রতার ভিত্তিতে:
* ক্ষুদ্র ভূমিকম্প (Microearthquake): সাধারণত অনুভূত হয় না। * লঘুমাত্রার ভূমিকম্প (Minor Earthquake): সামান্য অনুভূত হতে পারে। * মাঝারি ভূমিকম্প (Moderate Earthquake): মাঝারি ধরনের ক্ষতি হতে পারে। * গুরুতর ভূমিকম্প (Major Earthquake): ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারে। * মহাবিপর্যয়কর ভূমিকম্প (Great Earthquake): অত্যন্ত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায়।
ভূমিকম্পের প্রভাব
ভূমিকম্পের প্রভাবে নানা ধরনের ক্ষতি হতে পারে। এর কিছু প্রধান প্রভাব নিচে উল্লেখ করা হলো:
- জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি: ভূমিকম্পের কারণে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সেতু, ইত্যাদি ভেঙে গিয়ে অসংখ্য মানুষের জীবনহানি ঘটে এবং ব্যাপক সম্পত্তির ক্ষতি হয়।
- ভূ-ধস (Landslide): পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমিকম্পের কারণে ভূমিধস হতে পারে, যা রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিতে পারে এবং বসতি এলাকা ধ্বংস করতে পারে। ভূমিধস প্রবণ এলাকাগুলোতে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
- সুনামি (Tsunami): সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প হলে সুনামি সৃষ্টি হতে পারে, যা উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায়। সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র এ বিষয়ে নজর রাখে।
- ভূ-কম্পন (Liquefaction): ভূমিকম্পের সময় মাটি তার দৃঢ়তা হারাতে পারে এবং তরলের মতো আচরণ করতে শুরু করে, যার ফলে building collapse হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- আগুন (Fire): ভূমিকম্পের কারণে গ্যাস লাইন বা বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গিয়ে আগুন লাগতে পারে।
- নদীর গতিপথ পরিবর্তন (River Course Change): শক্তিশালী ভূমিকম্পের কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হতে পারে।
- মানসিক প্রভাব (Psychological Impact): ভূমিকম্পের শিকার হওয়া মানুষের মধ্যে মানসিক trauma সৃষ্টি হতে পারে।
ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপ
ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন স্কেল ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
- রিখটার স্কেল (Richter Scale): এটি ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপের সবচেয়ে পরিচিত স্কেল। এই স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ১ থেকে শুরু করে ৯ বা তার বেশি হতে পারে। চার্লস এফ. রিখটার এই স্কেল আবিষ্কার করেন।
- মার্সেলি স্কেল (Mercalli Scale): এটি ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির ওপর ভিত্তি করে তীব্রতা নির্ণয় করে। এই স্কেলে রোমান সংখ্যা ব্যবহার করা হয় (I থেকে XII)।
- মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল (Moment Magnitude Scale): এটি ভূমিকম্পের শক্তি পরিমাপের সবচেয়ে আধুনিক এবং নির্ভরযোগ্য স্কেল।
| মাত্রা | প্রভাব | 0-4.0 | মৃদু - সাধারণত অনুভূত হয় না, তবে যন্ত্রে ধরা পড়ে। | 4.1-5.0 | হালকা - অনুভূত হতে পারে, তবে তেমন ক্ষতি হয় না। | 5.1-6.0 | মাঝারি - কিছু ক্ষতি হতে পারে, যেমন - দেয়ালের ফাটল। | 6.1-7.0 | শক্তিশালী - মাঝারি থেকে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। | 7.1-8.0 | মারাত্মক - ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারে। | 8.1+ | মহাবিপর্যয়কর - অত্যন্ত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায়। |
ভূমিকম্পের পূর্বাভাস এবং সতর্কতা
ভূমিকম্পের সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস দেওয়া এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, তবে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেতে পারে:
- ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করা: যে সকল এলাকা ভূমিকম্প প্রবণ, সেখানে building code মেনে construction করা উচিত।
- সতর্কতা কেন্দ্র স্থাপন: ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে নিয়মিত seismic activity পর্যবেক্ষণ করা উচিত।
- জনসচেতনতা বৃদ্ধি: ভূমিকম্পের সময় কী করতে হবে, সে বিষয়ে জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা উচিত।
- ভূমিকম্প নিরোধক নির্মাণশৈলী (Earthquake Resistant Construction): ভূমিকম্প সহনশীল building design এবং construction techniques ব্যবহার করা উচিত।
- আর্লি warning system: ভূমিকম্পের প্রাথমিক তরঙ্গ সনাক্ত করে দ্রুত warning system চালু করা যেতে পারে।
ভূমিকম্পের সময় করণীয়
ভূমিকম্পের সময় শান্ত থাকা এবং সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া জীবন বাঁচাতে পারে:
- ভেতরে থাকলে:
* টেবিলের নিচে বা কোনো শক্ত furniture-এর আড়ালে আশ্রয় নিন। * মাথা ও ঘাড় হাত দিয়ে ঢেকে রাখুন। * জানালা, কাঁচের জিনিস, এবং ভারী জিনিস থেকে দূরে থাকুন। * বিদ্যুতের switch বন্ধ করুন এবং গ্যাস ভালভ বন্ধ করে দিন।
- বাইরে থাকলে:
* খোলা জায়গায় চলে যান। * building, গাছপালা, বিদ্যুতের তার এবং অন্যান্য hazard থেকে দূরে থাকুন।
- গাড়িতে থাকলে:
* গাড়ি থামিয়ে খোলা জায়গায় নেমে যান।
- ভূমিকম্প থেমে গেলে:
* সাবধানে building থেকে বেরিয়ে আসুন। * আহতদের সাহায্য করুন। * গ্যাস বা বিদ্যুতের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে কর্তৃপক্ষকে খবর দিন। * radio বা television-এর মাধ্যমে latest information-এর জন্য tune থাকুন।
বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকি
বাংলাদেশ ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল-এর মধ্যে অবস্থিত। এখানে plate boundary-গুলোর proximity-র কারণে ভূমিকম্পের ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে সিলেট এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভূমিকম্পের ঝুঁকি বেশি। ভূমিকম্প গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা করে।
উপসংহার
ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর ক্ষয়ক্ষতি কমাতে হলে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে। ভূমিকম্পের কারণ, প্রভাব এবং সতর্কতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অত্যন্ত জরুরি। নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়া-র মাধ্যমে জনগণের preparedness বাড়ানো যায়।
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ